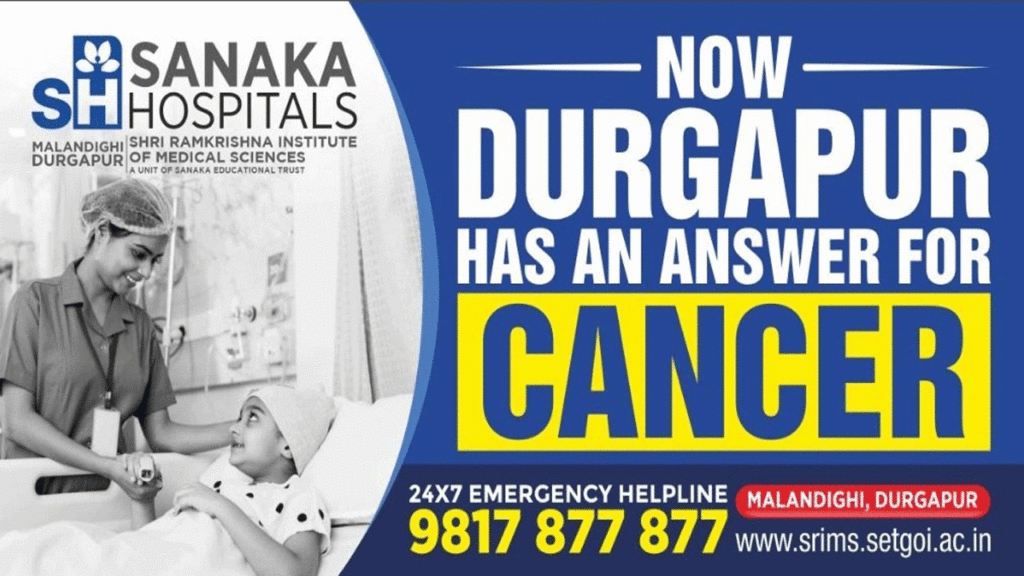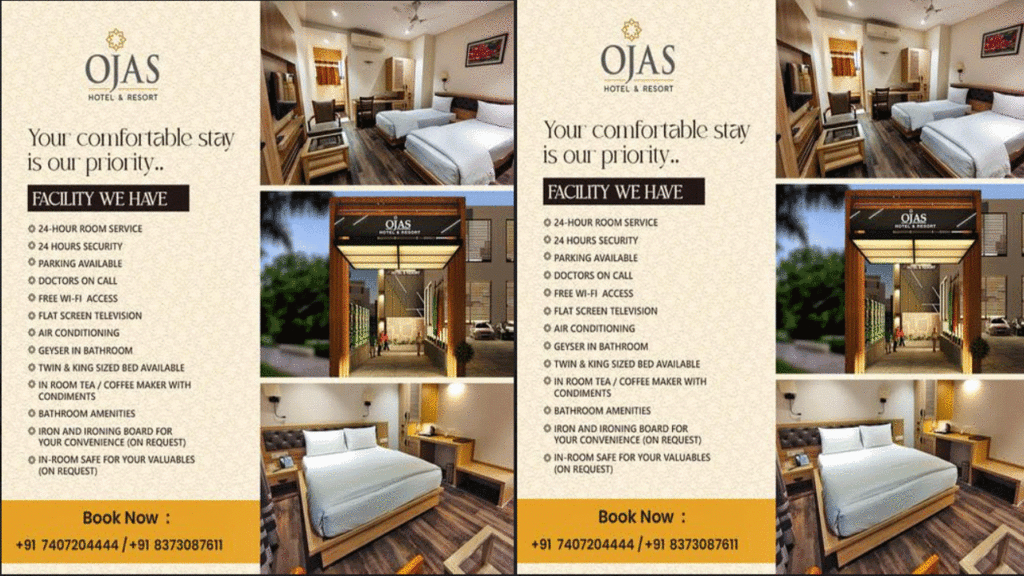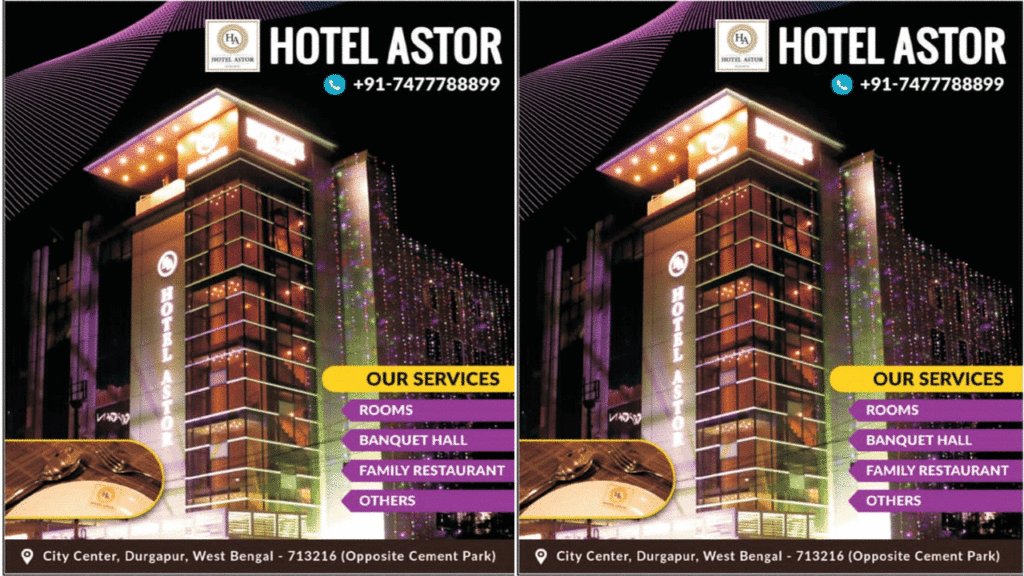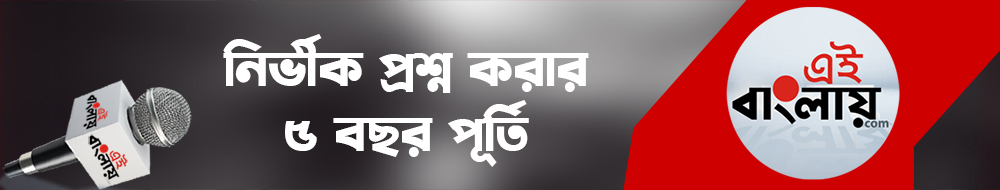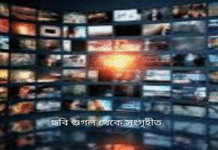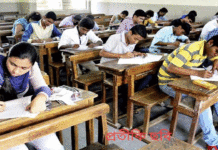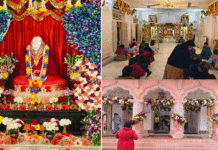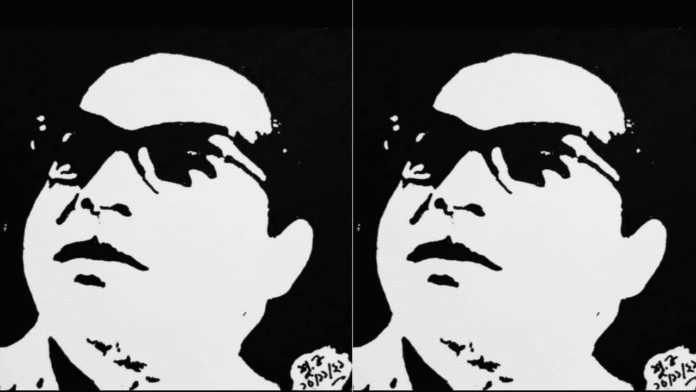ধ্রুপদ, ভক্তিগীতি, সিনেমার গান কিংবা আধুনিক — গানের সমস্ত শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। মাত্র ৭ – ৮ বছর বয়সের এই বালকের সংগীতে মুগ্ধ হয়ে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কৃত করেছিলেন তাঁকে। মাতৃ সাধনা এবং মাতৃ সঙ্গীতে নিবেদিত এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর মহাজীবন নিয়ে লিখলেন তাঁর বড়দা – সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের দৌহিত্র ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
‘সাধক রামপ্রসাদ’ ছবিতে মাত্র তেইশশো টাকা সম্মান দক্ষিণায় ২৩টি গান গেয়েছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ‘মুক্ত কর মা মুক্তকেশী’, ‘তিলেক দাঁড়া ওরে শমন’, ‘মা মা বলে আর ডাকব না’ – সঙ্গীতের আবেদন আজও অম্লান। আসলে এ যে শুধুমাত্র উপস্থাপিত সঙ্গীত নয়, তাঁর জীবন – জীবন সাধনা এবং মাতৃ সাধনার অমৃতধারা।
তিনি ছিলেন হাওড়ার পায়রাটুঙ্গির জমিদার পরিবারের সন্তান। এঁরা ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এই ভাদুড়ী বংশেরই মহান সন্তান ছিলেন চিরপ্রণম্য উদয়নাচার্য ভাদুড়ী। পার্বতীচরণ ভাদুড়ী এবং তাঁর ভ্রাতা কালীচরণ ভাদুড়ী – দুজনে ছিলেন এই ভাদুড়ী বংশের দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। দুজনেই ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সঙ্গীতেও ছিল তাঁদের আশ্চর্য দখল। এই পার্বতীচরণ ভাদুড়ী ছিলেন এই বংশের পুরুষোত্তম – ভাদুড়ী মহাশয় অর্থাৎ মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের পিতা। এই নগেন্দ্রনাথের রচিত এবং সুরারোপিত পরমার্থসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশীর সুমেরু মঠাধীশ শংকরাচার্য প্রমুখ ধর্মপ্রচারকরা নগেন্দ্রনাথকে ‘মহর্ষি’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁরাই নগেন্দ্রনাথকে ঘোষণা করেন পরমহংস হিসেবে। পরমহংস যোগানন্দ তাঁকে পরম শ্রদ্ধায় অভিহিত করতেন ভাদুড়ী মহাশয়ে নামে। পরমহংস যোগানন্দের লেখা পৃথিবী বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Autobiography of a Yogi ‘-র ‘The Levitating Saint ‘ – এই মহান যোগী নগেন্দ্রনাথেরই দিব্য জীবনের বর্ণনা। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের মেজদা নেপালচন্দ্রের পুত্র ননীলাল ভাদুড়ীও সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যের পথ বেছে নেন। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ তাঁকে ভাব সন্তানের মর্যাদা দেন। ব্রহ্মচর্য জীবনে ননীলালের নাম হয় ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।
পার্বতীচরণের ভ্রাতা কালীচরণের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের সন্তান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই ভাদুড়ী পরিবারের কেউ স্মৃতি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে বর্ধমান মহারাজার কাছ থেকে ভট্টাচার্য উপাধি পান। সেই ভট্টাচার্যই ব্যবহার করতেন এই সুরেন্দ্রনাথ। অনেক ছোটো বয়সেই সুরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই ভাদুড়ী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতান্তরের কারণে পূর্বপুরুষের বংশানুক্রমিক সম্পত্তি, একসময় জমিদারিরও অধিকার ছেড়ে দেন সুরেন্দ্রনাথ। পরে সাঁতরাগাছির গুরু পরিবারের নির্দেশে তিনি বিবাহ করেন অন্নপূর্ণা দেবীকে। তাঁদেরই তিন সন্তান বাংলা সঙ্গীত জগতের তিন চির উজ্জ্বল নক্ষত্র – সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, স্বর্ণকণ্ঠশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সাধক শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।
এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা একসময় নদিয়ার নবদ্বীপে অবস্থান করেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন রাজশাহী থেকে পাঁচশ বছর বা তারও কিছু সময় আগে। নবদ্বীপে থাকার সময় এঁরা তন্ত্রসাধনায় নিয়োজিত হন। যন্ত্রে মা কালীর নিত্য পুজো করতেন তাঁরা। পায়রাটুঙ্গিতেও নিজস্ব পুঁথি অনুসারে তন্ত্রোক্ত বিধি মেনে পুজো হতো এঁদের।
সুরেন্দ্রনাথের অকাল প্রয়াণের পর হাওড়ার বালিতে পারিবারিক গৃহ দেবতা বাণলিঙ্গের পুজোর ভার গ্রহণ করেন পরিবারের বড়ো ছেলে প্রফুল্ল ভট্টাচার্য। তিনি আজীবন কালীচরণের পূজিত বাণলিঙ্গ শিবেরই আরাধনা করেছিলেন। বালি বারেন্দ্রপাড়ার এই বাড়িতেই একসময় নিজের হাতে মা দক্ষিণা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাধক শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।
বাংলা সংগীত ধারার কিংবদন্তি প্রতিভা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাধনা ছিল দাদা প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের মতোই বৈধী মার্গের। কালীপুজোর আগের দিন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য সংযম করতেন। মায়ের পুজোর দিন নির্জলা উপোস করতেন। বাড়ির পুজো নিজেই করতেন। মাকে প্রদান করতেন এক সের রাবড়ি। তাঁর জলদ গম্ভীর কণ্ঠের সঙ্গীতে আর মন্ত্র উচ্চারণে মাতৃ আরাধনা যেন প্রতিমুহূর্তে পূর্ণতা পেতো। পুজো করতে করতে ভাব জগতে প্রবেশ করতেন তিনি। তাঁর সারা শরীর জুড়ে খেলা করতো দিব্য আলো।
পুজো সেরে প্রতি বছর নিয়ম করে তিনি পৌঁছে যেতেন শ্রীরামপুরে গঙ্গার পাড়ে শ্মশানের কালীপুজোয় গান গাইতে। পরে এখানে একটি বাড়িতে তিনি গান গাইতে যেতেন আমন্ত্রিত হয়ে। একবার সেখানেই তাঁর গানের রেকর্ডিং করা হয়। সেই রেকর্ডিং শোনার সময় দেখা যায় – তার গানের সঙ্গে আসছে ঘুঙুরের আওয়াজ। অথচ গান গাওয়ার সময় সেখানে তবলা ছিল। ঘুঙুর তো ছিল না!
(স্বর্ণকণ্ঠশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ছবিটি লেখকেরই আঁকা।)