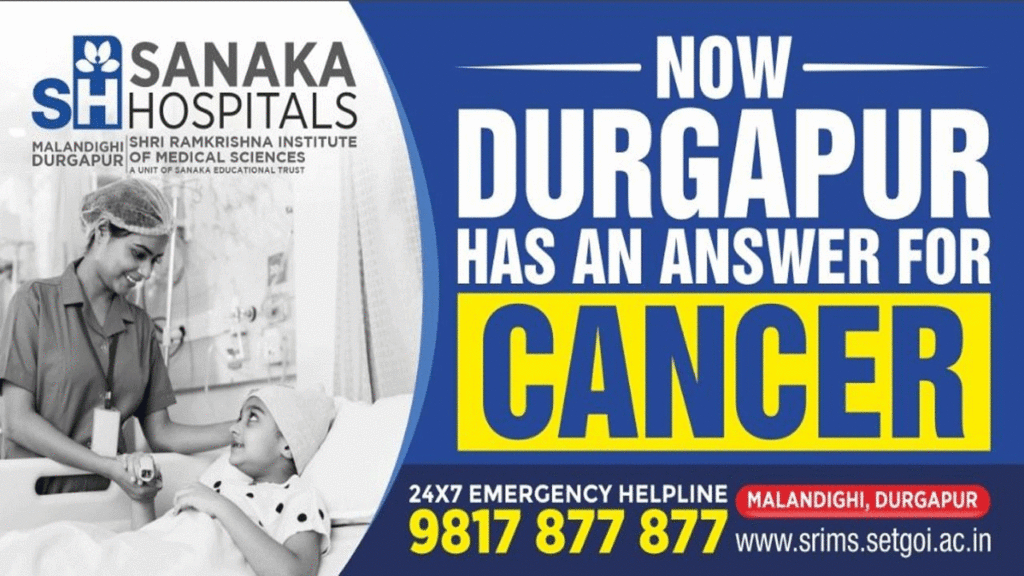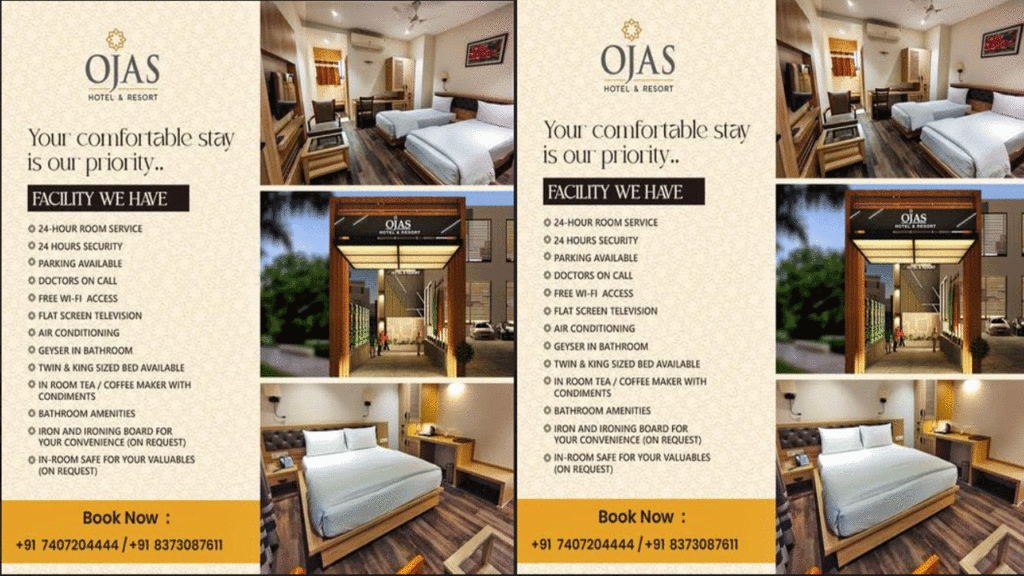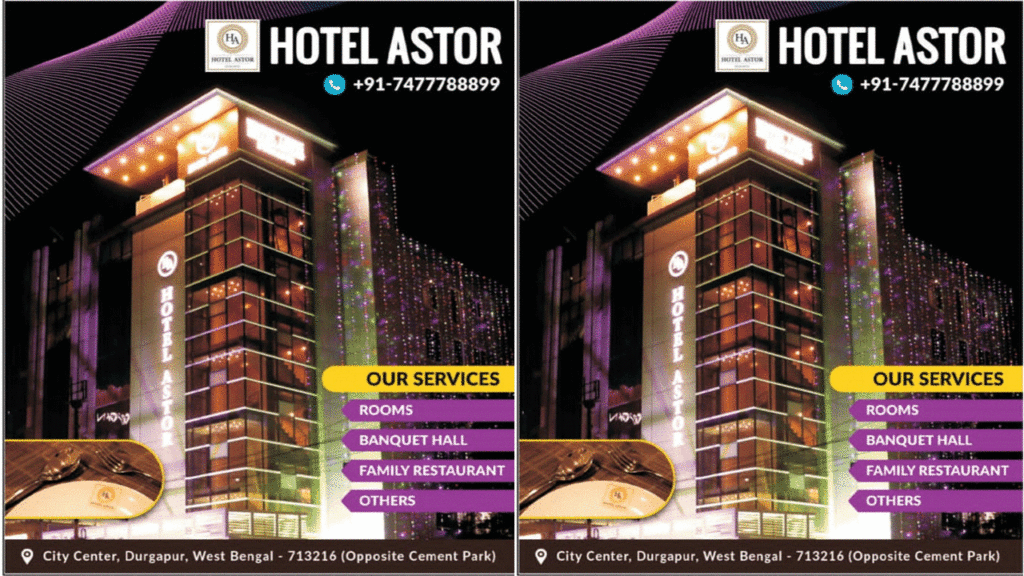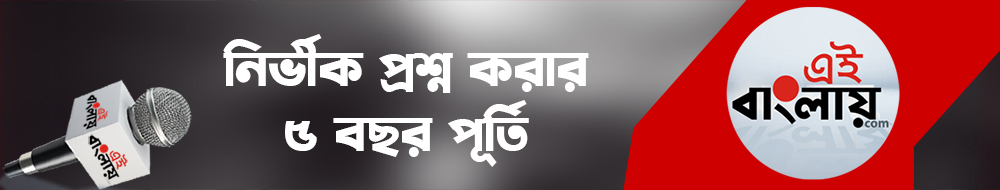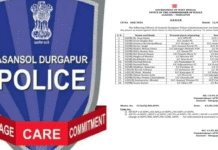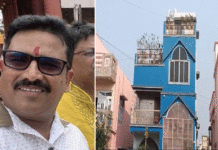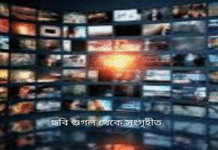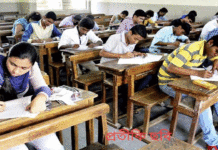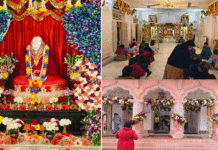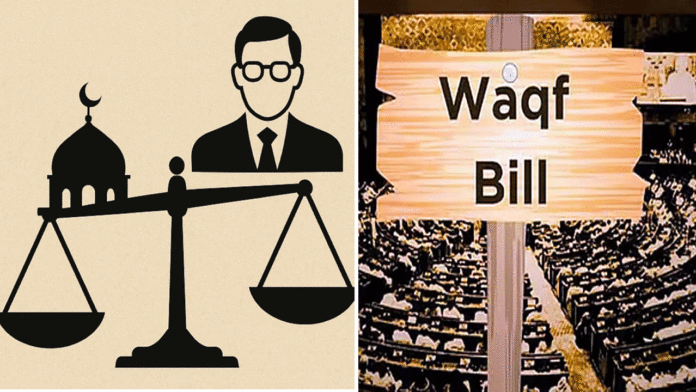দেবরাজ সাহাঃ- সব আইন কি শুধুই প্রশাসনিক যন্ত্র? অথবা কিছু কিছু আইন কি হয়ে ওঠে সময়ের স্পন্দন, সমাজের অন্তর্লীন উদ্বেগ, ধর্মীয় অধিকারের চুপিচুপি আত্মপ্রকাশ? পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদ্য উত্থাপিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল যেন সেই দ্বিতীয় ধরনেরই এক দলিল—যে নথিপত্রে শুধু জমি-সম্পত্তির হিসেব নয়, লেখা আছে সংখ্যালঘু সমাজের উদ্বেগ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং ধর্মের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের জটিল সম্পর্কের ইঙ্গিত।
ওয়াকফ, ইসলামী ঐতিহ্যে এক মহৎ দান—আল্লাহর নামে মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি। ভারতীয় বাস্তবতায় ওয়াকফের গুরুত্ব বহুমাত্রিক—মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য হাসপাতাল কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি এই সম্পত্তির উপরই গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থাপনার ভার বহন করে যে ওয়াকফ বোর্ড, তা কেবল প্রশাসনিক কাঠামো নয়—বরং ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের এক সাংবিধানিক রূপ।
তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার ভিত কেঁপেছে। বেড়েছে অভিযোগ—সম্পত্তি দখল, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব। সরকার বলছে, বহু দশকের সেই অনিয়মের অবসান ঘটাতে এই সংশোধনী বিল একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু সংখ্যালঘু সমাজের এক বড় অংশ তাতে দেখছেন এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ছায়া—যা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মপরিচয়ের পরিসরে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নির্দেশ করে।
প্রস্তাবিত বিলে রাজ্য সরকার ওয়াকফ বোর্ড গঠনে আরও সক্রিয় হবে। রেজিস্ট্রেশন, সম্পত্তির ব্যবহার, লিজ প্রক্রিয়া ইত্যাদিতে সরকারের নজরদারি দৃঢ় হবে। সরকারি ভাষ্যে এটি “সুশাসনের হাতিয়ার”। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়—একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি পরিচালনার পরিসরে রাষ্ট্রের প্রবেশ কি ন্যায্য? নাকি তা এক সাংবিধানিক ভারসাম্য লঙ্ঘনের দিকেই এগোচ্ছে?
বিরোধীরা বলছেন, এই বিল ভারতের সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের বিরোধী। যেখানে বলা হয়েছে, প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার রয়েছে। একজন বিরোধী বিধায়কের মন্তব্য, “ওয়াকফ বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ মানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্জলী যাত্রা। আজ মুসলিম, কাল অন্য গোষ্ঠীও পড়বে সেই শাসনছায়ায়।”
সমাজের ভেতর থেকেও উঠে আসছে নানা সুর। প্রবীণ ইমামদের কণ্ঠে এই বিল ঘিরে একধরনের আস্থা-চ্যুতি, তাঁরা মনে করেন—“ওয়াকফ সম্পত্তি আমাদের ধর্মীয় অস্তিত্বের অংশ। সরকারের দায়িত্ব সহযোগিতা করা, কর্তৃত্ব স্থাপন নয়।” আবার তরুণ সমাজকর্মীদের মধ্যে শোনা যায় এক পরিমিত দৃষ্টিভঙ্গি—“দুর্নীতির বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। যদি সরকার স্বচ্ছতা আনার নিরপেক্ষ কাঠামো তৈরি করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য। তবে সেই সিদ্ধান্ত যেন হয় সংলাপের মাধ্যমে, চাপিয়ে দেওয়ার নয়।”
এই দ্বৈত প্রতিক্রিয়া দেখায়—মুসলিম সমাজ নিজেও আত্মসমালোচনায় প্রস্তুত, স্বচ্ছতা চায়, কিন্তু চায় না নিজস্বতার বিনিময়ে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব। এ এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য—যেখানে প্রয়োজন প্রশাসনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা এবং সামাজিক শ্রদ্ধাবোধ।
আসলে এই বিল কেবল একটি আইন নয়—এ এক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রশ্ন। একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে টিকে থাকবে, সেই উত্তরেরই খোঁজ এটি। রাষ্ট্রের দায়িত্ব অপরিসীম—সে যেন স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার নামে আস্থার ভিত নষ্ট না করে। আর সংখ্যালঘু সমাজের দায়ও কম নয়—তাদের মধ্যে থেকেও উঠে আসুক সংস্কারের উদ্যোগ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
সরকারের উচিত ছিল একটি সমন্বিত নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু করা—যেখানে সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধিরা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং সমাজকর্মীরা একসাথে বসে ভাবতেন পরিবর্তনের রূপরেখা। অন্যদিকে, বিরোধীদেরও দরকার শুধু বিরোধিতা নয়, বিকল্প পথের প্রস্তাব—যেখানে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে এক পরিশীলিত সমঝোতা গড়ে ওঠে।
এই বিল এক নতুন প্রশ্ন তুলেছে—ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজের নিয়ন্ত্রণ কতটা হবে, আর রাষ্ট্রের ভূমিকাই বা কতটা হবে সেখানে? এ প্রশ্ন শুধু মুসলিম সমাজের নয়, এ প্রশ্ন সমগ্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার। কারণ একবার যদি ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপের ছাড়পত্র পায়, তবে তা যে কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে বিপজ্জনক উদাহরণ স্থাপন করতে পারে।
সুতরাং এই বিতর্ক একটি বৃহত্তর অন্বেষণের সুযোগ এনে দেয়—রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবার, সংস্কার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার। আইন তো কেবল কাঠামো, কিন্তু সেই কাঠামোর ভিত যদি গড়ে ওঠে আস্থার উপর, তবে তবেই তা হয় টেকসই ও অর্থবহ।
ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার দায় কেবল সংখ্যালঘু সমাজের নয়—এ আমাদের যৌথ ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার এক পরীক্ষা। রাষ্ট্র যদি সহযোগিতার হাত বাড়ায়, সমাজ যদি স্বচ্ছতার পথ বেছে নেয়, আর রাজনীতি যদি দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়—তবে এই সংশোধনী বিল কেবল বিতর্কের কেন্দ্রে নয়, হতে পারে ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি উন্নততর অধ্যায়ের সূচনা।